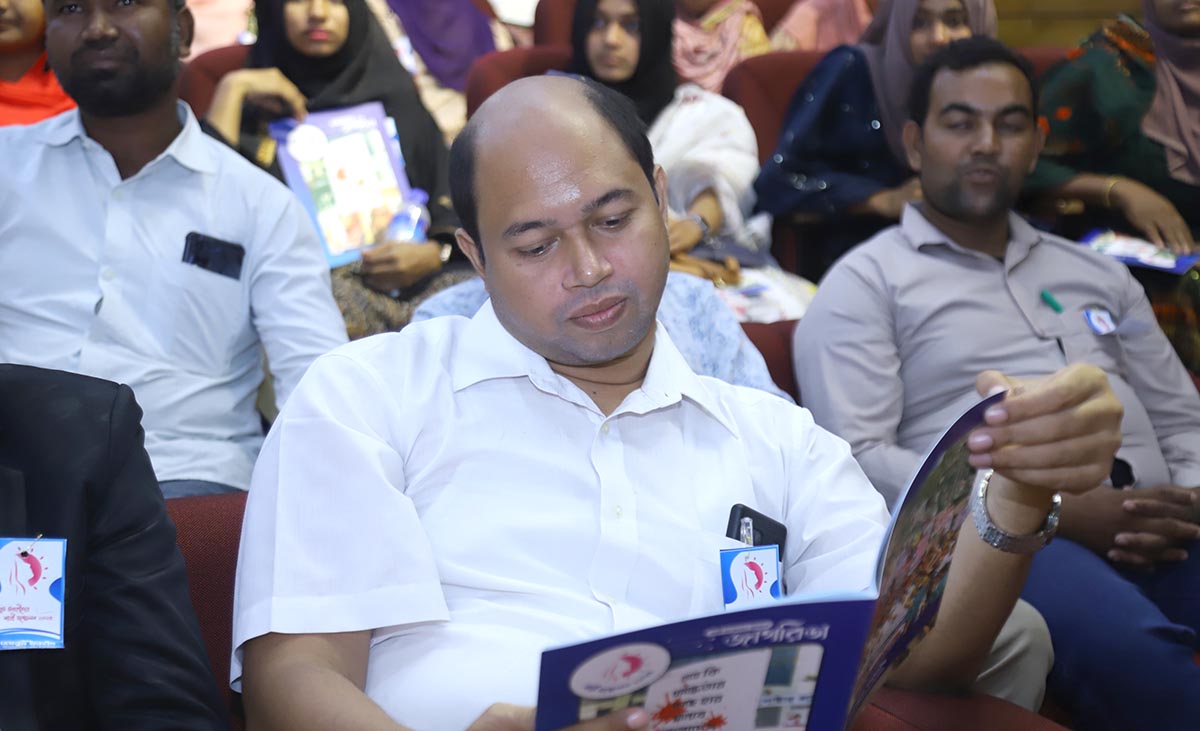

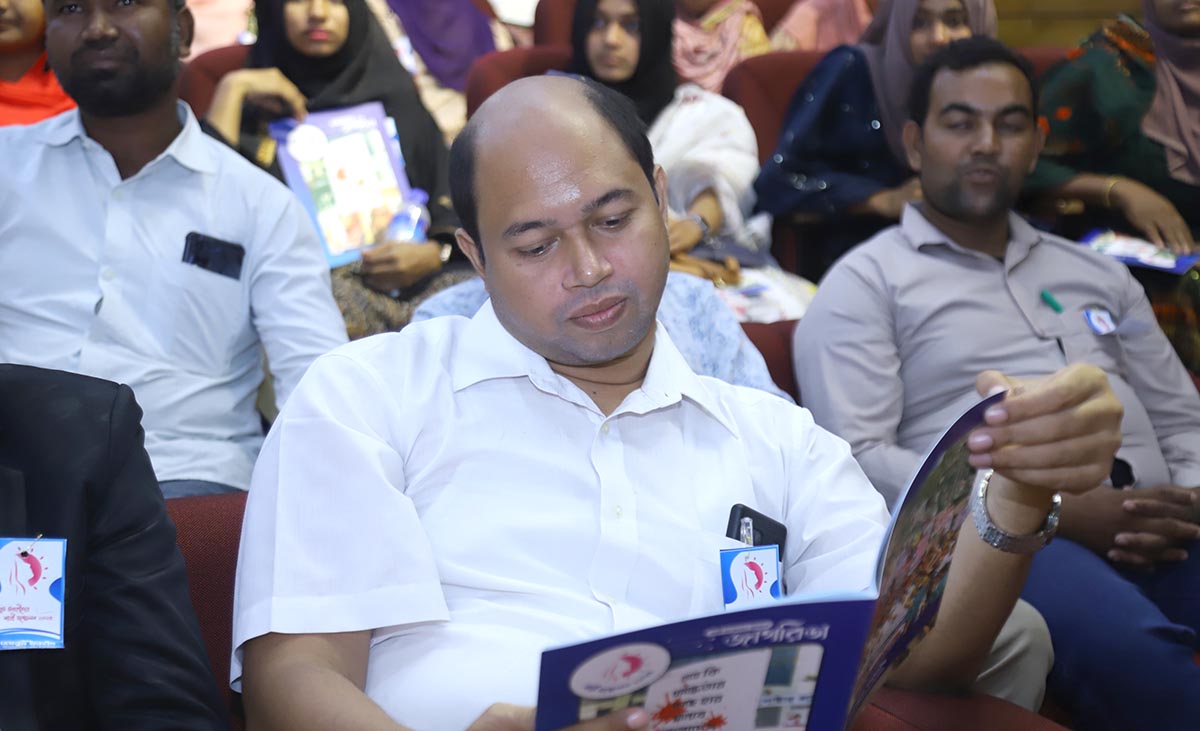
স্বাধীনতার অর্ধ-শতাব্দী পেরিয়ে এসে আমরা আমাদের পেছনে রেখে আসা রাজনৈতিক দিনলিপির দিকে তাকালে এর প্রতি পাতায় কেবল রক্তের দাগ দেখতে পাই। রক্তাক্ত লাশ, ক্ষমতার লড়াই, সন্ত্রাসবাহিনীর প্রতিপালন, অস্ত্র আর গোলাবারুদের গন্ধে আমাদের রাজনীতির অঙ্গন কলঙ্কিত। এদেশের মানুষ গণতন্ত্র বলতে বোঝে ভোট, আর ভোট বলতে বোঝে নেতাদের প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি আর রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক জিঘাংসার নগ্নরূপ। আমাদের দেশের রাজনীতির অঙ্গনটিতে কেন কোনো মানবতা বা সভ্যতার ছোঁয়া নেই, কেন এখানে এত সন্ত্রাস, সহিংসতা, দুর্নীতি, পেশীশক্তির দাপট? আসুন ফিরে যাই আরো পিছনে, আমাদের রাজনীতির উৎসমূলে।
এ কথা সকলেই জানেন যে, আমাদের দেশে প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা ব্রিটিশ শাসনামলের উত্তরাধিকার। ১৮৫৭ সনে সংঘটিত সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগ পর্যন্ত এই ভারত উপমহাদেশের শাসনকালকে ‘ব্রিটিশরাজ’ বলা হয়ে থাকে। আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা এ সময়েই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। যদিও সিপাহী বিদ্রোহেরও একশ বছর আগে থেকেই এদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে পরোক্ষভাবে ব্রিটিশ রাজত্বই চলে আসছিল, কিন্তু দিল্লির মসনদে আসীন ছিলেন মুঘল বাদশাহগণ, আর বিভিন্ন সুবায় ছিলেন নবাবগণ। যদিও তারা ছিলেন কোম্পানি ও অন্যান্য চক্রান্তকারীদের শিখণ্ডীমাত্র। ১৭৬৫ সালে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দিওয়ানি লাভের মাধ্যমে ‘অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দল’ হিসাবে কোম্পানির আবির্ভাব ঘটে এবং চূড়ান্ত পতন ঘটে দেশীয় রাজনীতির। সূত্রপাত হয় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের। খাজনা আদায় ও ব্যয়ের দায়িত্ব হাতে পেয়েই কোম্পানির লোকেরা অবাধ লুণ্ঠন ও অত্যাচার শুরু করে দেয়। ফলে মাত্র চার বছর যেতে না যেতেই ঘটে যায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, যে মহাদুর্ভিক্ষে প্রায় এক কোটি মানুষ না খেয়ে মারা যায়। জনৈক ইংরেজ কর্মকর্তা রেসিডেন্ট বেচার তার সরকারি পত্রে লিখেন, ‘দেশের অনেক জায়গায় সব কিছু খেয়ে শেষ করে এখন মানুষকে মানুষ আক্রমণ করছে ও খাচ্ছে।’ (বাংলার ইতিহাস ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো- প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম)।
এরপর ব্রিটিশ শাসকরা এদেশে তাদের শাসনকে চিরস্থায়ী করতে বহুমুখী ষড়যন্ত্রে মনোনিবেশ করে। বলাবাহুল্য তাদের শাসনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল এদেশের সম্পদ নিজেদের দেশে পাচার করে নিজ দেশকে সমৃদ্ধিশালী করে তোলা। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তারা এখানে গোড়া থেকেই ডিভাইড এন্ড রুল নীতি গ্রহণ করেছিল, অর্থাৎ এই ভারতবাসীকে যতভাগে ভাগ করা যায় তত সুবিধা। মুসলিমদের হাত থেকে তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিল। তাই মুসলিমরা যেন কোনোভাবে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে না পারে, তার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা হিসাবে তারা ১৭৮১ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার মাধ্যমে একটি বিকৃত বিপরীতমুখী ইসলাম শিক্ষা দিতে শুরু করল। এখানে রাখল না কোনো কর্মমুখী শিক্ষা, ফলে এখান থেকে পাস করে শিক্ষার্থীরা ধর্মকেই পুঁজি করে জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হল। ইউরোপীয় খ্রিষ্টান প্রাচ্যবিদগণ তাদের ক্ষুরধার মেধা খাটিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার সিলেবাস ও কারিকুলাম তৈরি করলেন এবং ১৪৬ বছর তারা নিজেরাই অধ্যক্ষপদে থেকে মুসলমানের সন্তানদেরকে ইসলাম শিক্ষা দিলেন। তারা শেখালেন যে একজন মুসলমানের মূল কাজ হচ্ছে আল্লাহর উপাসনা করা তথা নামাজ, রোজা করা, দোয়া-কালাম পাঠ করা, দাড়ি-টুপি রাখা। রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ে তাদের চিন্তা করার দরকার নাই, ওসব দুনিয়াদারীর বিষয় থেকে মুক্ত থেকে ব্যক্তিজীবনে একজন উত্তম মানুষ হওয়াই একজন মুসলমান হিসাবে তার বড় সার্থকতা। মুসলমানদেরকে বিশ্ব-সভ্যতার অঙ্গন থেকে পেছনে ছুঁড়ে ফেলার জন্য মাদ্রাসার সিলেবাসে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, পৌরনীতি, প্রযুক্তি, ভূগোল, শিল্প-সাহিত্য এসব বিষয় অন্তর্ভুক্তই করা হল না। আজও আমাদের মাদ্রাসাগুলো সেই ব্রিটিশ সিলেবাস অনুযায়ী চলছে এবং এখান থেকে যারা বের হয়ে আসছেন তাদের জ্ঞান অজু-গোসলের মাসলা মাসায়েলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।
খ্রিষ্টধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের জন্য তারা বহু অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মিশনারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিল। দ্যা চার্টার অ্যাক্ট অফ ১৮১৩ এর মাধ্যমে ঔপনিবেশিক সরকার ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য আনুষ্ঠানিক পদক্ষেপ নেয়। আর ১৮৩৫ সালে থমাস ব্যাবিংটন ম্যাকলে একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেন যা ‘দ্য ইংলিশ এডুকেশন অ্যাক্ট অফ ১৮৩৫’ নামে ভারতবর্ষসহ অপরাপর ব্রিটিশ উপনিবেশেও প্রবর্তন করা হয়। সেখানে ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে নির্ধারণ করা হয় এবং যেন ভারতীয়রা ব্রিটিশদেরকে দাপ্তরিক, ভূমি বন্দোবস্ত, রাজস্বের হিসাব-নিকাশ ও অন্যান্য স্থানীয় কাজে সহযোগিতা করতে পারে। মূলত হিন্দু জনগোষ্ঠীকে তারা এই শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে চাইল। এজন্য তারা প্রতিষ্ঠা করল হিন্দু কলেজ, সংস্কৃত কলেজ ইত্যাদি। এসব স্কুলে মুসলিম ছাত্রদের পাঠদানে ছিল বহুবিধ প্রতিবন্ধকতা। ব্রিটিশরা ডিভাইড এন্ড রুল নীতির বাস্তবায়নকল্পে তারা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি সৌহার্দ্যরে বন্ধনকে চূর্ণ করে দিতে সদা সচেষ্ট ছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে, সাহিত্যে, রাজনীতিতে তারা হিন্দু ও মুসলিম জনগোষ্ঠীকে অপরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপ্রবণ করে তুলল আর এই প্রক্রিয়া চলমান ছিল ব্রিটিশ রাজের অবসান না হওয়া পর্যন্ত। প্রাচ্যবিদেরা হাজার হাজার ইসলামবিদ্বেষী বই লিখলেন যা স্কুল কলেজে নিয়ম করে শেখানো হল। সেগুলো অনুবাদ করার জন্য এবং সেগুলোর আলোকে সাহিত্য রচনার জন্য তাদের সুবিধাভোগী বুদ্ধিজীবীরা আত্মনিয়োগ করলেন। মুসলিমরা হিন্দু সমাজ থেকে শিক্ষাদীক্ষায় একশ বছর পিছিয়ে পড়ল। কিছুদিন আগেই যারা ছিল ভারতবর্ষের শাসক তারা হয়ে গেল অসহায় সংখ্যালঘু। এগুলোই ছিল ব্রিটিশ প্রভুদের রাজনীতি-রাষ্ট্রনীতি।
কিন্তু একটা সময় ইংরেজদের বাইরের সভ্যতার মুখোস খসে বেরিয়ে এলো ভিতরের কদর্য কুৎসিত লোভী দানবের চেহারা। তাদের ও অধিকাংশ জমিদারদের শোষণে শাসনে ত্রাসনে পীড়নে মানুষের নাভিশ্বাস উঠে গেল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, সূর্যাস্ত আইন, কর্নওয়ালিস কোড, নীলকরদের শোষণের বিরুদ্ধে ধাপে ধাপে এদেশের মানুষ অধিকার সচেতন হতে শুরু করল। তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে শুরু করল। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিল মুসলিমরাই এবং সিপাহী বিপ্লবেও তাদের ভূমিকাই ছিল অগ্রগণ্য। ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলাসহ সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী এক সুসংগঠিত স্বাধীনতা আন্দোলন তাদের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল। এ আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন সৈয়দ আহমদ বেরেলভি। তিনি মুসলমানদের কাছে আমিরুল মোমেনীন হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তৎকালীন ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে শুরু করে মর্দান পর্যন্ত বিশাল অঞ্চলে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন ও ইসলামি শাসনব্যবস্থা চালু করেন।
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন নরমপন্থী এবং চরমপন্থী, অহিংস ও বৈপ্লবিক উভয় দর্শনের প্রচেষ্টায় এবং ভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করেছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মাধ্যমে রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে এই আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। ১৮৮৫ সালে ব্রিটিশ অবসরপ্রাপ্ত আইসিএস কর্মকর্তা অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউমের হাত ধরে এই রাজনৈতিক দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর নেতৃত্ব প্রদান করা হয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দাদাভাই নওরোজীসহ সেই শিক্ষিত শ্রেণিটির হাতে যারা মনেমগজে, চিন্তা-চেতনায় পুরোদস্তুর ইংরেজ। সরকারের সঙ্গে ভারতীয় স্বার্থ নিয়ে দেনদরবারের জন্য এমন লোকদেরকেই তারা পছন্দ করেছিল। তারা আন্দোলনের নামে মূলত প্রার্থনা, আবেদন-নিবেদন এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে এক মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছিল। তারা প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মত ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞেও ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থানে যেতে পারেনি। ধর্মনিরপেক্ষ দল হিসাবে কংগ্রেসে মুসলিম পরিবারের অনেকেই ছিলেন, কিন্তু নানাবিধ কারণে বৃহত্তর পশ্চাৎপদ মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষায় তেমন কোনো ভূমিকা রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এর প্রেক্ষিতে কংগ্রেস গঠনের ২১ বছর পর ১৯০৬ সালে ঢাকায় প্রগতিশীল মুসলিম শিক্ষাবিদ সৈয়দ আহমদ উল্লাহ, খাজা নবাব সলিমুল্লাহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ নিখিল ভারত মুসলিম লীগ নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করলেন। করটিয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নী (চান মিয়া)-ও এই দলে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।
উনিশ শতকের প্রথম ভাগে লালা লাজপত রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল যাদেরকে একত্রে লাল-বাল-পাল বলা হতো, সেই সঙ্গে শ্রী অরবিন্দ ঘোষ, মুসলিমদের মধ্যে আল্লামা এনায়েত উল্লাহ খান আল মাশরেকির এর বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার উপর আরও বেশি প্রভাব বিস্তার করছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ প্রান্তে কংগ্রেস অহিংস আন্দোলনের নীতিমালা অবলম্বন করেছিল এবং অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধী নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অথচ দু দুটো বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রায় ৩৫ লক্ষ ভারতীয় সৈনিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে লড়াই করেছে এবং ২ লক্ষাধিক প্রাণ হারিয়েছে, বিশ্বযুদ্ধের ব্যয় যোগাতে না খেয়ে মরেছে কোটি কোটি ভারতীয়। ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় তাদের অনুগত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা অপর্ণ করে যায়। আমাদের দেশের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলো সেই কংগ্রেস ও মুসলিম লীগেরই আধুনিক রূপ। তাদের ধমনীতে প্রবাহিত ব্রিটিশ রাজনীতি যেখানে সততার চেয়ে শঠতার কদর বেশি, মানবতার চেয়ে গালভরা কথার কদর বেশি। এখানে ধর্মকে ব্যবহার করা হয় ভোটের স্বার্থে, ধর্মের নামে ’৪৭ এ ব্রিটিশ প্রভুদের সুরে সুর মিলিয়ে উভয়দল যেমন দেশভাগকে অনিবার্য মনে করেছিল তেমনি এখনও আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিক দলগুলোর কাজের ফলে জাতি আজ বিভক্ত। কোনো জাতীয় স্বার্থ তাদেরকে এক করতে পারে না।
দীর্ঘদিন থেকে চলমান রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব পড়েছে আমাদের রোজকার বাজারে। প্রতিটি জিনিসের দাম বেড়েছে দ্বিগুণ, বাড়েনি মানুষের আয়। যুদ্ধ নিয়ে কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব চলছে আমাদের উপমহাদেশেও। একদিকে চিন অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্র, মাঝে চিড়েচ্যাপ্টা বাংলাদেশ। ঘনিয়ে আসছে কঠিন দুঃসময়। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় আছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ফলে অস্তিত্বের সংকটে পড়ে গেছে তিনবার সরকার গঠনকারী দল বিএনপি। অতীতের প্রতিটি নির্বাচন আমাদের বলে দেয়, আবারও বাংলাদেশের রাজপথ রক্তে পিচ্ছিল হতে চলেছে। যখন দেশের আকাশে ডানা মেলেছে পরাশক্তিধর শকুন, তখন নিজেদের মধ্যে হানাহানি করে শকুনের খাদ্যে পরিণত হওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত? ব্রিটিশদের শেখানো বিভাজনের রাজনীতির শেষ পরিণতি কী হয় তা আমাদের অজানা নয়। আমাদের সামনে আছে সিরিয়া, ইরাক, লিবিয়া, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তানের মত উদাহরণ। তাদের হাতে বিপুল পরিমাণ গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র জমা হয়ে আছে, সেগুলো বিক্রি করার জন্য প্রয়োজন যুদ্ধক্ষেত্র। চিন ও ভারতের নিকটবর্তী হওয়ায় আমাদের এই ভূখণ্ডটি যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও চিন সবার জন্যই লোভনীয়। উপরন্তু আমাদের মাটির নিচে আছে বিপুল খনিজ সম্পদ, আমাদের আছে সতেরো কোটি মানুষের বাজার, আমাদের দেশে আছে দীর্ঘ সমুদ্র উপকূল। সব মিলিয়ে আমাদের দেশটি ছোট হলেও কূটনৈতিক দাবাখেলায় গুরুত্বপূর্ণ ঘুঁটি। আমরা যদি গণতন্ত্রের নামে বিভক্তি টিকিয়ে রাখি আর নিজেরা নিজেরা হানাহানিতে ব্যস্ত থাকি, তাহলে খুব সহজেই আমাদের বহু রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনত, সার্বভৌমত্ব, নিজেদের এক টুকরো মাটি আবারও বিদেশী শক্তির করতলগত হয়ে যাবে। তখন না থাকবে আওয়ামী লীগ, না থাকবে বিএনপি। তখন সবাই হব নিজভূমে পরবাসী, আমাদের সোনার বাংলা হবে চিন অথবা যুক্তরাষ্ট্রের বলয়ে অবস্থিত তাদের নব্য উপনিবেশ।
[লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট
যোগাযোগ: mdriazulhsn@gmal.com
ফোন: ০১৭১১-০০৫০২৫, ০১৭১১-৫৭১৫৮১, ০১৬৭০-১৭৪৬৪৩]